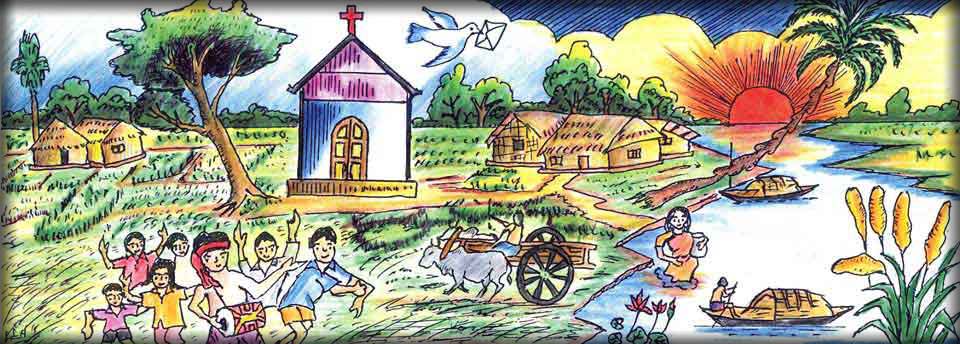ফাদার সাগর কোড়াইয়া
যিশুর জন্মের জুবিলীবর্ষ পালন করছে বিশ্বমণ্ডলী। এ উপলক্ষে সারা পৃথিবী থেকে খ্রিস্টভক্তগণ ভাটিকানে তীর্থে যাচ্ছে। বাংলাদেশের খ্রিস্টানরাও এর বাইরে নয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দল ভাটিকানে তীর্থ করে ফিরে এসেছে। জুবিলীবর্ষ হচ্ছে নবায়িত হওয়ার সময়। নবায়িত হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে তীর্থস্থান পরিদর্শন। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোতে তীর্থ করার প্রচলন বেশ প্রাচীন। হিন্দুধর্মে কাশী, বৃন্দাবন ও পুরী তীর্থ করার অন্যতম স্থান। একইভাবে ইসলাম ধর্মে মক্কা-মদিনায় হজ পালন, বৌদ্ধ ধর্মে লুম্বিনী, বোধগয়া, সারনাথ, শ্রাবস্তীসহ আরো অসংখ্য তীর্থস্থান রয়েছে। আর খ্রিস্টধর্মে জেরুসালেম ও রোমে তীর্থভ্রমণ অন্যতম।
 তীর্থভ্রমণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি, পাপমোচন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ, ঈশ্বর ধর্মবোধের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়ানো সম্ভব হয়। অনেকের জন্য তীর্থযাত্রা একটি আচার হিসাবে স্বীকৃত। আবার অনেকের নিকট এটি আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত পুরষ্কার সন্ধানের সাথে জড়িত। তীর্থ সাধারণত একা অথবা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ, গন্তব্যে পৌঁচ্ছানো, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, বস্তু এবং স্থাপত্যের মুখোমুখি হওয়া, বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নিজ গন্তব্যে ফিরে আসা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বলেন, তীর্থযাত্রা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশের একটি পথ, বিশ্বাসের যাত্রা এবং জীবনের প্রতীক। তিনি আরো বলেন, তীর্থযাত্রা ছুটি কাঁটানোর মত বিষয় নয়; বরং পবিত্র বস্তু ও স্থানে তীর্থযাত্রা করে বিশ্বাসের প্রকাশ।
তীর্থভ্রমণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি, পাপমোচন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ, ঈশ্বর ধর্মবোধের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়ানো সম্ভব হয়। অনেকের জন্য তীর্থযাত্রা একটি আচার হিসাবে স্বীকৃত। আবার অনেকের নিকট এটি আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত পুরষ্কার সন্ধানের সাথে জড়িত। তীর্থ সাধারণত একা অথবা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ, গন্তব্যে পৌঁচ্ছানো, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, বস্তু এবং স্থাপত্যের মুখোমুখি হওয়া, বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নিজ গন্তব্যে ফিরে আসা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বলেন, তীর্থযাত্রা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশের একটি পথ, বিশ্বাসের যাত্রা এবং জীবনের প্রতীক। তিনি আরো বলেন, তীর্থযাত্রা ছুটি কাঁটানোর মত বিষয় নয়; বরং পবিত্র বস্তু ও স্থানে তীর্থযাত্রা করে বিশ্বাসের প্রকাশ।
তীর্থযাত্রা হলো একটি ভক্তিমূলক অনুশীলন যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘযাত্রা যা প্রায়শই পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ গন্তব্যের দিকে পরিচালিত হয়। এটি একটি সহজাতভাবে ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতা, যা অংশগ্রহণকারীকে বাড়ির পরিবেশ এবং পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তীর্থযাত্রা করার উপায় বা প্রেরণা ভিন্ন হতে পারে, তবে কাজটি শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়কে একীভূত অভিজ্ঞতায় মিশ্রিত করে। একজন বিশ্বাসী তার মানত পূরণ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাভ, ইতিবাচক ঘটনার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে তীর্থযাত্রা করতে পারেন। মণ্ডলীর ইতিহাসে ইউরোপের দেশগুলোতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে তীর্থযাত্রা করার রীতি প্রচলিত ছিলো। বিশেষ করে অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর জনগণ তীর্থযাত্রা করতো। দ্বাদশ শতাব্দীকে মূলত খ্রিস্টিয় তীর্থযাত্রার স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে পরবর্তী শতাব্দী জুড়ে এটি একটি ভক্তিমূলক অনুশীলন হিসাবে রয়ে গিয়েছে।
৩২৭-৩২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট সাধু কনস্টানটাইনের মা সাধ্বী হেলেন মণ্ডলীর ইতিহাসে জেরুসালেম নগরীতে প্রথম তীর্থ করেন। তিনি যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর স্থানে তীর্থ করে যিশুর ক্রুশ আবিষ্কার করেন। একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে, সাধ্বী হেলেন জেরুসালেমে তীর্থ করতে গিয়ে অসংখ্য ক্রুশ আবিষ্কার করেছিলেন। আর এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় যিশু ছাড়া আরো অনেককেই ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তবে অসংখ্য ক্রুশের মধ্যে কোনটি যিশুর ক্রুশ তা বুঝতে পারছিলেন না। তাই সাধ্বী হেলেন একটি কাজ করেন। রোগীদের এনে প্রত্যেকটি ক্রুশ স্পর্শ করান। আর আর্শ্চয্যের বিষয়, একটি ক্রুশ স্পর্শ করলেই রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। আর এ থেকে তিনি ধারণা করে নেন যে, ঐ ক্রুশটিই হচ্ছে যিশুর ক্রুশ। এরপর সাধ্বী হেলেন ক্রুশটি রোম নগরীতে নিয়ে আসেন।
ইদানিং বাংলাদেশ মণ্ডলীতে হরহামেশাই যে কোন স্থানকেই তীর্থস্থান হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, অনলাইন, প্রিন্ট মিডিয়াগুলোতে মহাসমারোহে তীর্থস্থান ও তীর্থোৎসব শব্দটি চাক্ষুস। আর ভক্তবিশ্বাসীদের মধ্যে বিষয়টা এমনভাবে গ্রথিত হচ্ছে যে, তারাও তীর্থ, তীর্থস্থান ও তীর্থোৎসব বলেই জানে। দেখা যাচ্ছে কোন ধর্মপল্লীর পর্ব উৎসব কিন্তু সবাই বলছে তীর্থোৎসব। চাইলেই কি যে কেউ যে কোন স্থান, ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানকে তীর্থস্থানরূপে ঘোষণা করার অধিকার রাখে; নাকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট কারণে কোন স্থানকে তীর্থস্থান ঘোষণা করতে পারে। নিশ্চয়ই যথাযথ একটি আইন বা নীতিমালা রয়েছে আর না থাকলে থাকাটা আবশ্যিক। জনগণকে অবগত করা জরুরি যে, কোনটা তীর্থোৎসব, তীর্থস্থান, কোনটি পর্ব আর মহাপর্ব।
মাণ্ডলিক আইনের ১২৩০ থেকে ১২৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করতে পারেন। অর্থাৎ কোন গির্জা, ধর্মপল্লী, এলাকা বা অঞ্চল তীর্থস্থান হতে গেলে স্থানীয় মণ্ডলীর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মৌখিক বা লিখিত ঘোষণাপত্রের প্রয়োজন রয়েছে; তবে এর জন্য যথাযথ কারণ প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ। আর এই তীর্থস্থান বা তীর্থোৎসব ঘোষণা স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হতে পারে। কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ষকে কেন্দ্র করে অনেক ধর্মপ্রদেশ বছরব্যাপী তীর্থ ঘোষণা করে থাকে। এছাড়া জাতীয় তীর্থস্থান ঘোষণার জন্য স্থানীয় বিশপ সন্মিলনীর অনুমোদন ও পোপের দপ্তরে আবেদন অপরিহার্য। আমাদের একটি ধারণা আছে যে, চাইলেই তীর্থস্থান বা তীর্থোৎসব বলা ও করা যায়। তবে এর উত্তর হচ্ছে কখনোই না। তীর্থস্থান হতে গেলে অবশ্যই এর মূলে বা পূর্বে এক বা একাধিক আশ্চর্যকাজ থাকতে হবে। এছাড়াও তীর্থস্থান সে স্থানকেই বলা হবে যেখানে একজন সাধু-সাধ্বী, ধর্মশহীদ অথবা কুমারী মারীয়ার সাথে সম্পর্কিত কোন ঘটনা রয়েছে।
 বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তীর্থস্থান হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। বিশেষ করে, পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থ ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবাই বটতলাতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ অন্যতম। এই দুটি স্থানে তীর্থস্থান হবার পিছনে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আশ্চর্যকাজ রয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারি, চট্রগ্রামের দিয়াং এবং দিনাজপুরের রাজারামপুরে যে তীর্থোৎসব হয় তা ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশের মতো ছোট্র দেশের ছোট কাথলিক মণ্ডলীতে এত তীর্থস্থান ঘোষণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। ইদানিং আরো অনেক স্থানে স্বঘোষিত তীর্থ, তীর্থস্থান এবং তীর্থোৎসবের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তীর্থস্থান হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা পূর্ণ হচ্ছে না কোনভাবেই।
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তীর্থস্থান হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। বিশেষ করে, পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থ ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবাই বটতলাতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ অন্যতম। এই দুটি স্থানে তীর্থস্থান হবার পিছনে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আশ্চর্যকাজ রয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারি, চট্রগ্রামের দিয়াং এবং দিনাজপুরের রাজারামপুরে যে তীর্থোৎসব হয় তা ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশের মতো ছোট্র দেশের ছোট কাথলিক মণ্ডলীতে এত তীর্থস্থান ঘোষণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। ইদানিং আরো অনেক স্থানে স্বঘোষিত তীর্থ, তীর্থস্থান এবং তীর্থোৎসবের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তীর্থস্থান হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা পূর্ণ হচ্ছে না কোনভাবেই।
কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষাতে বলা হয়েছে, “তীর্থযাত্রা এই পৃথিবীতে আমাদের যাত্রাকে স্বর্গের দিকে যাত্রার অর্থ বহন করে, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রার্থনায় নবীকরণ আনয়নের জন্য বিশেষ সুযোগ দান করে; কেননা জীবন্ত জলের অন্বেষণকারী তীর্থযাত্রীর জন্য তীর্থস্থানগুলো খ্রিস্টমণ্ডলীর অভ্যন্তরে খ্রিস্টিয় প্রার্থনার বিভিন্ন ধরন অনুসারে জীবনযাপন করার বিশেষ স্থান”| শিল্পীর গান, “তীর্থে কেন যাবে রে মন, তীর্থ গোটা দুনিয়াটা” বুঝি আজ বাস্তব সত্য। এই বাক্যের অন্তর্নির্হিত তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে পারলে কোনটি তীর্থ, তীর্থস্থান এবং তীর্থোৎসব তার অর্থ আরো স্পষ্ট হবে।