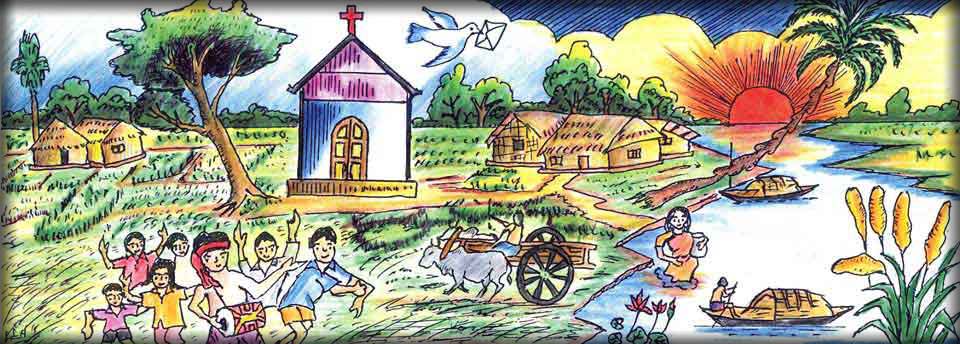জন-জীবনের কথা
ফাদার সাগর কোড়াইয়া
 ছাইকে আমরা অবহেলার বস্তু হিসাবেই জানি। কথার ফাঁকে করো ওপর বিরক্ত হলে বলি ‘দূর ছাই’। অর্থাৎ ছাই যেমন অবহেলা বা বিরক্তজনক বস্তু তেমনি ব্যক্তিটিও ছাইয়ের সমতুল্য। ছাইকে আমরা যতই অবহেলা করি না কেন ছাই নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাইয়ের নানাবিধ গুণাগুণ রয়েছে। শহরাঞ্চলগুলোতে ছাই বিক্রিও করা হয়। ঢাকাতে থাকাকালীন এক বাসায় গিয়েছি। বাসায় বসে থেকেই শুনতে পেলাম ছাই বিক্রেতা মহিলা অভিনব সুরে চিৎকার করে ছাই বিক্রি করছে। আমার ধারণা ছিলো না যে, ছাইও বিক্রি হয়। কৌতুহলবশত জানালার ফাঁক গলে উঁকি দিলাম। মধ্যবয়ষ্ক একজন মহিলা প্লাস্টিকের বস্তায় ছাই ভরে মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেককে আবার ছাই কিনতেও দেখলাম।
ছাইকে আমরা অবহেলার বস্তু হিসাবেই জানি। কথার ফাঁকে করো ওপর বিরক্ত হলে বলি ‘দূর ছাই’। অর্থাৎ ছাই যেমন অবহেলা বা বিরক্তজনক বস্তু তেমনি ব্যক্তিটিও ছাইয়ের সমতুল্য। ছাইকে আমরা যতই অবহেলা করি না কেন ছাই নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাইয়ের নানাবিধ গুণাগুণ রয়েছে। শহরাঞ্চলগুলোতে ছাই বিক্রিও করা হয়। ঢাকাতে থাকাকালীন এক বাসায় গিয়েছি। বাসায় বসে থেকেই শুনতে পেলাম ছাই বিক্রেতা মহিলা অভিনব সুরে চিৎকার করে ছাই বিক্রি করছে। আমার ধারণা ছিলো না যে, ছাইও বিক্রি হয়। কৌতুহলবশত জানালার ফাঁক গলে উঁকি দিলাম। মধ্যবয়ষ্ক একজন মহিলা প্লাস্টিকের বস্তায় ছাই ভরে মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেককে আবার ছাই কিনতেও দেখলাম।
যাই হোক- গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেই মায়েদের প্রথম কাজই হলো চুলার ছাই তোলা। ছাই উপকারী পদার্থ হলেও তা সংগ্রহের যে উপকরণ তা আবার ভাঙ্গা কোন মাটির পাতিলের অংশবিশেষ হয়ে থাকে। অন্যদিকে ছাই আবার ফেলা হয় বাড়ির বাহিরে অবহেলিত কোন স্থানে। ছাই এত অবহেলার হলেও এমন কিছু বিশেষ কাজে ছাই ব্যবহৃত হয় যা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব হয় না। বিশেষভাবে ছাই দিয়ে দাঁত, হাঁড়ি-পাতিল মাজা হয়। জমিতে ছাই ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়ানো ও জমিতে কীটনাশক হিসাবে ছাইয়ের ব্যবহার একটি প্রাচীন কৃষি চিকিৎসা ব্যবস্থা। মাছ কুটতে ছাইয়ের ব্যহারের জুড়ি মেলা ভার। ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে ছাই ব্যবহার করে শুষ্কতা আনা হয়। এগুলো ছাড়াও ছাই হয়তো আরো নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।
সপ্তাহে বুধবার একবার আসে। আর বছর হিসাব করলে অসংখ্য বুধবার পুঞ্জিকাতে ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে মণ্ডলিতে ভস্মবুধবার বছরে একবারই আসে। মণ্ডলিতে ভস্মবুধবার ভস্ম লেপনের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশের রীতি প্রচলিত। তবে ভস্ম মাখানোর ইতিহাস বেশী পুরাতন নয়। একাদশ শতাব্দিতে ভস্মবুধবারে ছাই লেপনের রীতি চালু হয়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ভস্ম শরীরে মেখে উপবাস বা ত্যাগস্বীকার করার উদাহরণ রয়েছে। প্রবক্তা দানিয়েলের পুস্তকের নবম অধ্যায়ে ছাই মেখে উপবাস করার কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, ছাই লেপন হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন। ভস্মবুধবারে ছাই লেপনের সাথে সাথে উচ্চারিত বাক্য “হে মানব মনে রেখো তুমি ধুলি আর ধুলিতেই মিশে যাবে” মর্ত্যরে মানুষকে জন্ম ও মৃত্যুর পরের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়।
বিশ্বের বৃহৎ ধর্মগুলোর প্রবর্তক, মুণি-ঋষিগণ মহৎকাজে প্রবেশের পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত ও উপবাস করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। যিশুখ্রিস্ট তাঁর প্রচার কাজ আরম্ভের পূর্বে মরুভূমিতে ৪০ দিন উপবাস করেছেন। মরুভূমির বাস্তবতা হলো- যেদিকেই চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। তাই এই ৪০ দিনের উপবাসে যিশুর শরীর ভস্মের পরিবর্তে নিশ্চয়ই বালিতে ভরপুর হয়ে গিয়েছিলো। অনেক সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে উপবাস করার রীতি প্রচলিত ছিলো। যিশুর যন্ত্রণা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্যে প্রবেশের পূর্বে খ্রিস্টভক্তদেরও উপবাসের মধ্য দিয়ে চল্লিশদিন অতিবাহিত করতে হয়। তাই উপবাস দেখানোর কোন বিষয় নয় “তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভন্ডদের মতো বিষন্ন ভাব দেখিয়ো না” (মথি ৬:১৬)। বরং উপবাস হচ্ছে নিজের খারাপ কিছু পরিত্যাগ করে ভালোর সাথে সন্ধি স্থাপন। তবে ব্যক্তিবিশেষে উপবাস ভিন্ন ধরণের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপবাস এমনই হওয়া উচিৎ যা উপবাসের পর মানুষকে নতুন জীবন দান করে। আবার এমনও লোক দেখা যায়, যিনি উপবাস অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ঠিকই কিন্তু জীবনের রূপান্তর ঘটে না।
তপস্যাকাল মানুষকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পথ দেখায়। যে তিনটি কাজ মানুষের জন্য কঠিন সেই তিনটি কাজ উপবাস, প্রার্থনা ও দয়াদানে মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করতে মাতা মণ্ডলি খ্রিস্টভক্তদের অনুপ্রাণিত করে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে খাদ্যের প্রতি দূর্বল তাই সীমিত আহার অর্থ্যাৎ উপবাস, প্রার্থনায় অমনোযোগীতা পরিহার করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রার্থনায় মনোনিবেশ ও দয়াদান বা দয়াভিক্ষা অর্থ্যাৎ যা অন্যকে দেবার ফলে নিজের কষ্ট হবে জেনেও নিঃস্বার্থভাবে দেওয়াই হয়ে উঠতে পারে তপস্যাকালের স্বার্থকতা। তপস্যাকালের এই তিনটি শুদ্ধিক্রিয়া মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে। তবে উপবাস আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় সুস্থ্যতায় অপরিহার্য। উপবাস মানুষকে সংযম শেখায়। তাই উপবাস আমাদের জন্য একটি বড় পাওয়া। কিন্তু অনেক সময় আমরা উপবাস শুধুমাত্র আহার গ্রহণ থেকে বিরত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। উপবাস যে আরো অনেকভাবে হতে পারে তা হয়তো উপলব্দিতে আনি না।
ভস্ম থেকে ভস্মবুধবারের আধ্যাত্মিকতা আসে। আর ভস্মবুধবারের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালের পূর্ণতা পায়। সাধারণ একটি দিন কিভাবে কপালে ভস্মের স্পর্শে অসাধারণ হয়ে ওঠতে পারে তা ভস্মবুধবারেই স্পষ্ট হয়। যে ভস্ম তুচ্ছ হিসাবে বিবেচ্য সে ভস্মই কপালে স্পর্শ ও বাক্যে পবিত্র হয়ে ওঠে। ভস্ম লেপনের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশ করে নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণই যেন হয় সবার আধ্যাত্মিক সাধনা।